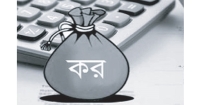প্রকাশ : ০২ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৫৭
চিরায়ত বাঙালির সম্প্রীতির শারদীয়া

জগৎ সৃষ্টির মূলসূত্র সম্প্রীতি। পাতালে-পবনে, অবণী ও অন্তরীক্ষের সর্বত্রই সম্প্রীতির সম্মিলন। সম্প্রীতি যেখানে নেই, সৃষ্টি সেখানে বিপন্ন। সম্প্রীতি আছে বলেই স্রষ্টার সৌন্দর্য আছে, সৃষ্টি ও স্রষ্টার সমন্বয় আছে। নবগ্রহের সম্প্রীতিতে সৌরজগত অটুট আছে আজও। সূর্যের সাত রঙে সম্প্রীতি সুসংহত বলেই সাদা রঙের রৌদ্রস্নানে পৃথিবী সবুজ রূপ নিয়ে শস্যবতী হয়। সম্প্রীতির কারণেই রংধনুর সাতরং বৃষ্টির কণাকে গোল করে তাকে বর্ণিল করে তোলে। জগতের এই সম্প্রীতি মানুষকেও মুগ্ধ করে তোলে। হাতের পঁাচ আঙ্গুলের সম্প্রীতিতেই আমরা অন্ন গ্রহণ করি। মন ও মস্তিষ্কের সম্প্রীতি ও সমন্বয়ে আমরা চলি জীবনের পথ। বাংলাদেশের ষড়ঋতু সম্প্রীতির সমন্বয় মেনে চলে বলেই কেউ প্রখর রোদে পুড়িয়ে মারলে কেউ এসে নবধারাজলে সিক্ত করে তোলে। কেউ আকাশকে মসীমাখা করে গেলেও আর কেউ এসে তা সংস্কার করে নীলবর্ণ ফেরত দিয়ে যায়। কেউ এসে কনকধান্যে অঞ্জলি দিয়ে গেলে কেউ এসে হিমের হাওয়ায় রিক্ত করে দিয়ে যায়। দিনশেষে বসন্ত এসে মলয়ের মাধুর্যে মন মাতিয়ে যায়। সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার, ভক্তের সাথে ভগবানের সম্প্রীতি আছে বলেই ভক্তের পূজায় ভগবান বর দেন, আশিসের ডালি ভরিয়ে দেন।
ভক্ত আর ভগবানের সম্প্রীতি সম্মিলনীর এক অনন্য ঋতু শরৎ। প্রকৃতিতে শরৎ হচ্ছে আবাহনের ঋতু। অনেক বছর আগে শরৎ ছিলো আশীর্বাদের ঋতু। কাউকে সে সময় আশীর্বাদ করতে হলে বলা হতো, শত শরৎ বেঁচে থাকো। কেননা, বছর শুরু হতো মার্গশিরার অগ্রহায়ণে আর শেষ হতো শরৎ ঋতুর অন্তিমে কার্তিকে। প্রখর রোদ, নীল আকাশ, সাদা মেঘের কুলপি বরফ ভেলা আর নদীর তীরজুড়ে অবাধ্য কাশের সমাহারে শরৎ আসে কৈলাশকন্যার আগমনী নিয়ে। তঁার আগমনের মাঝে সম্প্রীতির সমারোহ উছলে পড়ে। পুত্র-কন্যা, বিদ্যা-বৈভব আর সিদ্ধি-সমরের সাথে আসে শত্রু অসুর, শিরোধার্য শিব। সিংহবাহিনীর আগমন মানেই ধনী-দরিদ্র, সম্ভ্রান্ত-সর্বস্বান্ত সবারই উৎসব। এর চেয়ে বড়ো সম্প্রীতি আর নেই কোথাও।
উৎসবের সার্বজনীনতা বজায় রাখতেই দেবী দুর্গা হয়ে উঠেন বাঙালি মা। মায়ের কাছে রামও যা রহিমও তা। ব্রাহ্মণ যা চন্ডালও তা। তাইতো অষ্টোত্তর শতনামধারী মায়ের প্রতিমায় নয় ধরনের নারীর গৃহদ্বারের মৃত্তিকা আবশ্যক হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণী, মালিনী, গোয়ালিনী, ধোপিনী, শূদ্রানী, নাপতানী, কাপালিনী, নর্তকী আর বারবনিতার দ্বারের মাটি না হলে তঁার প্রতিমার অবয়ব তৈরি হয় না। এ নয় নারীর গৃহদ্বারের মাটির সমন্বয়ে যে মৃন্ময়ী তৈরি হয়, সে বোধনের মাধ্যমে হয়ে উঠে চিন্ময়ী। তখন সকল নদীর ধারা সমুদ্রে মিশে যাওয়ার মতো সকল ক্ষুদ্র মিলে পরমে বিলীন হওয়ার মাতৃরূপ জীবন্ত হয়ে উঠে। সর্বজনীন সম্প্রীতির যে রূপের মধ্য দিয়ে শারদীয়ায় ফুটে উঠে তা অনিন্দ্য ও অতুলনীয়। নব রাত্রিতে মায়ের নয় রূপ ভিন্ন ভিন্নভাবে সম্মিলিত হয়ে তৈরি করে নবদুর্গার শক্তিসম্ভার। দেবীপক্ষের প্রথম দিনে সে শৈলীপুত্রী, দ্বিতীয় দিনে ব্রহ্মচারিণী, তৃতীয় দিনে চন্দ্রঘন্টা, চতুর্থ দিনে কুষ্মাণ্ডা, পঞ্চম দিনে স্কন্ধমাতা, মহাষষ্ঠীতে কাত্যায়নী, মহাসপ্তমীতে কালরাত্রি, মহাষ্টমীতে মহা গৌরী এবং মহানবমীতে সিদ্ধিদাত্রীর রূপ নিয়ে আবির্ভূতা হন। এই নবরূপের সমন্বিত সম্প্রীতিই হলো মাতৃরূপিনী দুর্গা, যে দুর্গতিনাশিনী। শুধু দেবীরূপেই নয়, তার প্রসাদে নবরূপ থেকেও বুঝা যায়, শারদীয়া আসে সম্প্রীতির সার্বজনীনতা নিয়ে। নবরাত্রিতে মায়ের নয় রকম প্রসাদ। প্রথম রাত্রিতে ঘি, দ্বিতীয় রাত্রিতে চিনি, তৃতীয় রাত্রিতে ক্ষীর বা পায়েস, চতুর্থ রাত্রিতে মালপোয়া, পঞ্চম রাত্রিতে কলা, মহাষষ্ঠীতে মধু, মহাসপ্তমীতে নারকেল, মহাষ্টমীতে হালুয়া এবং মহানবমীতে ডালিম। রংয়ের দিক থেকেও দেবী দুর্গা সম্প্রীতি ও সমন্বয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন। তঁার প্রিয় রং
দেবিপক্ষের প্রথম দিন হলুদ, দ্বিতীয়ায় সবুজ, তৃতীয়ায় খয়েরি, চতুর্থীতে গেরুয়া বা কমলা, পঞ্চমীতে সাদা, মহাষষ্ঠীতে লাল, মহাসপ্তমীতে নীল, মহাষ্টমীতে গোলাপি এবং মহানবমীতে বেগুনি। দেবীর এই যে বর্ণসমন্বয়, এতে প্রমাণিত হয়, দেবী কেবল অসুর বিনাশিনীই নন, দেবী সম্প্রীতি সংহিতা। তঁার স্নান ও মহাস্নানে ব্যবহার্য জলের রকমফেরেও তিনি বুঝিয়ে দেন, তিনি কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের দেবী নন। তিনি সকলের মা, তিনি সকলের বিপদনাশিনী, মঙ্গলদায়িনী। আটঘড়া জলে তঁার যে মহাস্নান তাতে থাকে গঙ্গা জল, শঙ্খ জল, তীর্থ জল, কবোষ্ণ জল, সুগন্ধি জল, শুদ্ধ জল, পুষ্পোদক, নারকেল জল বা ফলোদক, শিশির জল, বৃষ্টি জল ও সাগর জল।
জগজ্জননী দুর্গার পূজা বারোয়ারি পূজা বলেই, আনন্দ-উৎসব গৃহে নয়, আঙ্গিনা ও মণ্ডপে মণ্ডপে শোভিত হয়। গলিতে-ঘাটায় ঢাকের বাদ্যে উপচে পড়ে খুশি। উৎসবের মুখ্য চেতনা হলো সম্প্রীতি। এখানে জ্ঞানের সাথে ধনের যেমন সম্প্রীতি ঘটে, তেমনি সনাতনের সাথে আধুনিকতারও সমন্বয় ঘটে। সর্বাধুনিক বিশ্বাস আর সনাতনী বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ নয় বরং প্রীতির বন্ধনে অটুট মানবিকতাকে প্রকট করাই হলো উৎসবের উদ্দেশ্য। আরতির মধ্যে তাই আর ধর্ম মুখ্য থাকে না, তা হয়ে যায় সংস্কৃতি। মা শারদীয়ার উৎসবের মধ্য দিয়ে নারীর ক্ষমতায়নকেই মুখ্যত প্রস্ফুটিত করা হয়। বাঙালি নারীরা অবলা ও কোমল। নিজেদের জীবনের সিদ্ধান্ত তারা নিজেরা নিতে পারে না। এসব কোমলপ্রাণ নারীদের মধ্যে শক্তির সঞ্চার করতে শক্তির আধাররূপে মা দুর্গার মতের্য অবতরণ।
পূজোর আয়োজন হলো একটা মঞ্চ। এ মঞ্চ সম্প্রীতির, এ মঞ্চ হলো সম্মিলনের। দল বেঁধে একপাড়ার ভক্ত অন্য পাড়ায় যায়। এই যাওয়া-আসায় হিংসার অবলোপন হয়, বিভেদের দ্বন্দ্ব দূর হয়। ঠাকুরের দর্শনে পাড়ায় পাড়ায় সম্প্রীতি তৈরি হয়। প্রতিযোগিতা থাকে, কিন্তু প্রতিহিংসা থাকে না। রাষ্ট্রীয় কূটনীতির কারণে আন্তঃধর্মীয় সংহতিতে রাজনীতি ঢুকে যায়। ফলে সংখ্যাগুরুর দাপটের ভেতর দিয়ে অসুরের আস্ফালন শুরু হয়। কিন্তু দিনশেষে সম্প্রীতির কথা বলে সাম্প্রদায়িক অসুরদের চিহ্নিত করা হয়। সাম্প্রদায়িক অসুরেরা চেষ্টা করে রাজনীতির ক্রীড়নক হয়ে সম্প্রীতিকে খণ্ড-বিখণ্ড করতে। তবু শিষ্টের মঙ্গল ইচ্ছাই প্রাধান্য পায়।
কৃষিভিত্তিক বাঙালি সমাজে মায়েরা যেন দশহাতসম্পন্না। তারা ভোরে অরুণের উদ্বোধন হতে শুরু করে রাতে শয্যাগত হওয়া অবধি দশভুজার মতোই কাজ করে। তাই তাদেরকে তুলনা করা হয় স্বয়ং দুর্গারূপে। দেবী দুর্গার ভিন্ন নাম হলো সতী, সাধ্বী। তিনি কন্যা, প্রৌঢ়া এমনকি যুবতী বা কৈশোরী নামেও পরিচিতা। তিনি কুমারী রূপেও বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন নামে পূজিতা হন। তিনি এক বছর বয়সী কন্যারূপে সন্ধ্যা, দুই বছরে সরস্বতী, তিন বছরে ত্রিধামূর্তি, চার বছরে কালিকা, পঁাচ বছরে সুভগা, ছয় বছরে উমা, সাত বছরে মালিনী, আট বছরে কুঞ্জিকা, নয় বছরে কালসন্দর্ভা, দশ বছরে অপরাজিতা, এগারো বছরে রুদ্রাণী, বারো বছরে ভৈরবী, তেরো বছরে মহালক্ষ্মী, চৌদ্দ বছরে পঠিনায়িকা, পনেরো বছরে ক্ষেত্রজ্ঞা এবং ষোলো বছরে অম্বিকা নামে পূজোপ্রাপ্ত হন। এ ছাড়াও দেবী দুর্গা শঙ্করের সঙ্গিনী বলে শঙ্করী, দেবতা বা সুরের ঈশ্বরী বলে সুরেশ্বরী, গণেশের মা বলে মহোদরী এবং পাতালে গায়ত্রী নামে পূজিতা। যে নামেই দুর্গাকে ডাকি না কেন, বাঙালি জীবনে দুর্গা হলো দুর্গতিনাশিনী এবং মহিষাসুর মর্দিনী।
দুর্গা অস্ত্রধারী যেমন তেমনি মঙ্গলধারীও। দুর্গার পূজায় নয়টি উদ্ভিদের পাতার উপকরণ লাগে যা নবপত্রিকা নামে পরিচিত। কলাপাতা , সাদা অপরাজিতা, হলুদ , জয়ন্তী, বেলপাতা, দাড়িম্ব, অশোক, মানকচু ও ধান এই নবপত্রিকার নয়টি উদ্ভিদ আসলে দেবী দুর্গার নয়টি বিশেষ রূপের প্রতীকরূপে কল্পিত হয়। এই নয় দেবী হলেন রম্ভাধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাণী, কচ্বাধিষ্ঠাত্রী কালিকা, হরিদ্রাধিষ্ঠাত্রী উমা, জয়ন্ত্যাধিষ্ঠাত্রী কার্তিকী, বিল্বাধিষ্ঠাত্রী শিবা, দাড়িম্বাধিষ্ঠাত্রী রক্তদন্তিকা, অশোকাধিষ্ঠাত্রী শোকরহিতা, মানাধিষ্ঠাত্রী চামুন্ডা ও ধান্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী। এই নয় দেবী একত্রে ‘নবপত্রিকাবাসিনী নবদুর্গা’ নামে পূজিতা হন।
শারদীয়ার আবাহন মূলত আবহমানকালের বাঙালিয়ানারই বহিঃপ্রকাশ, যা উৎসবময়তাকে প্রকাশিত করে। বাঙালি সর্বদাই সমাজবদ্ধ জীব। বাঙালির গোষ্ঠীপ্রীতি ও উৎসবপ্রীতি যে কোনো উছিলাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। শারদীয় দুর্গা পূজাও বাঙালির উৎসবপ্রীতির অনন্য নিদর্শন। দেবী দুর্গার আখ্যানে যেমন অসুরের উপস্থিতি লক্ষণীয়, তেমনি বাঙালি সমাজেও কতিপয় সাম্প্রদায়িক অসুরের কুকর্মের নিদর্শন আমরা প্রতিবছর দেখতে পাই। শরতের শুরুতে নির্মীয়মাণ দুর্গা প্রতিমায় আঘাত করে এরা নিজেদের অসুরত্বের পরিচয় তুলে ধরে। এদের অন্তর্চক্ষুতে জ্ঞানের সম্মিলন ঘটিয়ে সম্প্রীতির মঙ্গলময়তায় শতভাগ শুভ হোক শারদীয়ার মতর্যাগমন-- এই হোক শারদাবাহনের মূল প্রতিপাদ্য। শুধু রণক্ষেত্র জয় নয়, হৃদয়ক্ষেত্র জয় করে অমঙ্গলবিনাশিনী দুর্গা বাঙালিকে সম্প্রীতির মেলবন্ধনে বেঁধে রাখুক চিরকাল। ভ্রাতৃঘাতী বিভাজন দূর হোক, মনুষ্যত্বের জয়গানে সম্প্রীতিময় হয়ে উঠুক শারদমাতার মতর্যাভিযান।