প্রকাশ : ১০ জানুয়ারি ২০২৪, ০০:০০
দ্রুতগতির ডেটা ট্রান্সফার প্রযুক্তি
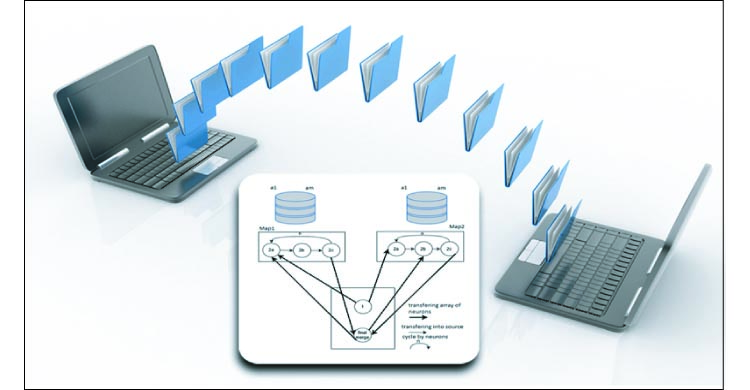
বর্তমান বিশ্বে দ্রুত ডেটা স্থানান্তরের মাধ্যম হলো অপটিক্যাল ফাইবার। এই ফাইবার মানুষের চুলের ১০ ভাগের এক ভাগ পাতলা এবং আলোর গতিতে দূরবর্তী স্থানে ডেটা পাঠায় আলোকে সিগন্যাল হিসেবে ব্যবহার করে। সম্প্রতি জাপানের গবেষকরা অপটিক্যাল ক্যাবলের এই দ্রুতগতির সঙ্গে ডেটার পরিমাণও বহুগুণে বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। এজন্য তারা ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সিং প্রযুক্তি ব্যবহার করেছেন। একে ওয়েভ ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিংও (ডব্লিউডিএম) বলা হয়। এই প্রযুক্তির সাহায্যে অনেক কমিউনিকেশন সিগন্যাল রূপান্তরিত হয় সিঙ্গেল ট্রান্সমিশনে।
অতঃপর পেটাবিটস গতিতে ডাটা ট্রান্সফার করে। এক পেটাবিটস সমান ১০ লাখ গিগাবিটস (১ পেটাবিট = ১০০০ টেরাবাইট বা ১ কোয়াড্রিলিয়ন বিটস)। ডব্লিউডিএম প্রযুক্তিতে বর্তমানে প্রতি সেকেন্ডে ২২.৯ পেটাবিটস (বা ২২ হাজার ৯০০ টেরাবিট) গতিতে ডাটা স্থানান্তর করতে সক্ষম। এই প্রযুক্তির আগের ডেটা ট্রান্সফারের হার ছিল প্রতি সেকেন্ডে ১০.৬৬ পেটাবিটস। তথ্য আদান-প্রদানের ডাটার ক্ষুদ্র একক হলো বিট। সেজন্য ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিডের একককেও বিট (নঢ়ং -নরঃ ঢ়বৎ ংবপড়হফ) বলা হয়।
প্রতিসেকেন্ডে যে পরিমাণ ডেটা বিট স্থানান্তরিত হয়, তার পরিমাণকে নঢ়ং বলে। শুরু থেকে ডেটা ট্রান্সমিশনের হিসাবটি করা হয় এভাবে- আট (৮) বিটে এক (১) বাইট, ১০২৪ বাইটে এক কিলোবাইট (কই), ১০২৪ কিলোবাইটে এক মেগাবাইট (গই), ১০২৪ মেগাবাইটে এক গিগাবাইট (এই), ১০২৪ গিগাবাইটে এক টেরাবাইট (ঞই), ১০২৪ টেরাবাইটটে এক পেটাবাইট (চই), ১০২৪ পেটাবাইটে এক এক্সাবাটাবাইট (ঊই), ১০২৪ এক্সাবাটাবাইটে এক জেটাবাইট (তই), ১০২৪ জেটাবাইটে এক ইয়টাবাইট (ণই)।
কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং সিস্টেম চালুর প্রথম থেকেই বিট পার সেকেন্ড হিসেবে ইন্টারনেট স্পিড পরিমাপ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় সমস্ত ডেটার আপলোড এবং ডাউনলোডের গতি বিট হিসাবে প্রদর্শিত হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ নঢ়ং যখন ডেটা ট্রান্সমিশনের গতির একক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তখন সেটিকে ব্যান্ডউইথ বলা হয়। সাধারণত ডেটা ট্রান্সফার গতির ওপর ভিত্তি করে ডাটা ট্রান্সমিশন স্কিডকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন- ১. ন্যারো ব্যান্ড, ২. ভয়েস ব্যান্ড, ৩. ব্রড ব্যান্ড। ন্যারো ব্যান্ড সাধারণত ৪৫ থেকে ৩০০ নঢ়ং পর্যন্ত হয়ে থাকে।
ধীর গতিতে ডেটা স্থানান্তরের জন্য ব্যবহার করা হয় এই ব্যান্ড। ভয়েস ব্যান্ড- ফ্রিকোয়েন্সিগুলোর ব্যাপ্তি সাধারণত মানুষের কাছে শ্রবণযোগ্য। এই ব্যান্ডের ডেটা স্থানান্তর গতি ৯৬০০ নঢ়ং পর্যন্ত হয়ে থাকে। এটি সাধারণত টেলিফোনে বেশি ব্যবহার করা হয়। ব্রড ব্যান্ড- ব্রডব্যান্ড হলো প্রশস্ত ব্যান্ডউইথ ডেটা ট্রান্সমিশন, যা একাধিক সিগন্যাল এবং বিভিন্ন ট্রাফিক পরিবহন করে। এই ব্যান্ড ডেটা স্থানান্তর গতি কমপক্ষে ১গনঢ়ং হতে অত্যন্ত উচ্চগতি পর্যন্ত হয়ে থাকে। ব্রডব্যান্ড ডেটা ট্রান্সমিশনে সাধারণত কো-এক্সিয়াল ক্যাবল ও অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করা হয়।
তথ্য আদান-প্রদানের এই হিসাবের সঙ্গে ‘কোড ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাকসেস (সিডিএমএ)’, ‘ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাকসেস (এফডিএমএ)’, ‘টাইম ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাকসেস (টিডিএমএ)’ এবং ‘গ্লোবাল সিস্টেম ফর মোবাইল কমিউনিকেশন (জিএসএম)’ ইত্যাদি নানা প্রযুক্তি জড়িত। সিডিএমএ হলো ডিজিটাল সেলুলার প্রযুক্তি টেলিযোগাযোগে ব্যবহৃত ভয়েস, ডেটা এবং অন্যান্য ডিজিটাল তথ্য বেতার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রেরণের জন্য। এটি একাধিক অ্যাক্সেস কৌশলগুলোর মধ্যে একটি, যা চ্যানেলগুলো বরাদ্দ করতে এবং একাধিক ব্যবহারকারীকে একই সঙ্গে একই ফ্রিকোয়েন্সি স্পেকট্রাম ভাগ করার অনুমতি দেয়।
জিএসএম হচ্ছে এফডিএমএ এবং টিডিএমএ-এর সম্মিলিত একটি চ্যানেল অ্যাকসেস পদ্ধতি। বাংলাদেশে টেলিটক, গ্রামীণফোন, বাংলালিংক ও রবি (অধুনালুপ্ত এয়ারটেলসহ) মোবাইল অপারেটর জিএসএম প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে। ১৯৯১ সালে জিএসএম কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে জিএসএম প্রযুক্তি মোবাইল ফোনের ক্ষেত্রে ব্যবহার শুরু হয়। জিএসএম প্রযুক্তি এখনো বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় মোবাইল নেটওয়ার্ক, যা ২১৮টি দেশে ব্যবহৃত হয়। এ প্রযুক্তিতে আন্তর্জাতিক রোমিং সুবিধা বেশি পাওয়া যায়। সিম (ঝওগ) সহজলভ্যতার কারণে ব্যবহারকারীগণ ইচ্ছামতো জিএসএম নেটওয়ার্ক এবং হ্যান্ডসেট বা মোবাইল সেট পরিবর্তন করতে পারে।
এ প্রযুক্তি মোবাইল ডেটা ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে উচ্চগতির প্রযুক্তি জিপিআরএস (জেনারেল প্যাকেট রেডিও সার্ভিস) ও ইডিজিই (এনহ্যানসড ডেটা রেট ফর জিএসএম ইভুলোশন) সুবিধা প্রদান করে। এর সেল কাভারেজ এরিয়া এখন পর্যন্ত কমবেশি ৩৫ কিলোমিটারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবে এতে বিদ্যুৎ খরচ তুলনামূলকভাবে বেশি, যা গড়ে প্রায় ২ ওয়াট। যেখানে সিডিএমএ টেকনোলজির ক্ষেত্রে গড়ে মাত্র ২০০ মাইক্রোওয়াট। এর ডেটা ট্রান্সফার রেট তুলনামূলক কম, যা ৫৬ শনঢ়ং। জিএসএম এ পালস টেকনোলজি ব্যবহারের কারণে হাসপাতাল, এরোপ্লেন প্রভৃতি স্থানে মোবাইল ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা থাকে।
দ্রুতগতির এই ডাটা ট্রান্সমিশন প্রক্রিয়া কাজে লাগাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে নাসা বিজ্ঞানীরা তাদের টেলিস্কোপ নিয়ন্ত্রণে। মহাবিশ্ব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯০০ বর্গমাইল জুড়ে গড়ে উঠেছে এই টেলিস্কোপ, যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতে ১ বিলিয়ন পিসির সমান সুপার কম্পিউটার আছে। ১.৩ মিলিয়ন টেলিস্কোপের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই প্রজেক্টের নাম ‘স্কয়ার কিলোমিটার অ্যারে (এসকেএ)’। যা মহাবিশ্ব সম্পর্কে নানা অমীমাংসিত বা অনুত্তরিত প্রশ্নের সমাধান দেবে কয়েক সেকেন্ড।
ডব্লিউডিএম প্রযুক্তির সহায়তায় ১৫ মিটার উঁচু স্যাটেলাইটগুলো মহাশূন্যে নির্গত ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন শনাক্ত করতে পারবে মুহূর্তেই। এছাড়াও ৫০ আলোকবর্ষ দূর থেকেও পৃথিবীর এয়ারপোর্ট রাডারকে শনাক্ত করতে সক্ষম হবে এই প্রযুক্তি। ফলে, স্যাটেলাইটগুলো প্রতিসেকেন্ডে কয়েক পেটাবিটস ডাটা তৈরি করতে সক্ষম হবে, যা বর্তমান বিশ্বের ইন্টারনেট ট্র্যাফিক থেকে ১০০ গুণ বেশি দ্রুত হবে।
এই ডেটাগুলো প্রতিদিন ৬৪ গিগাবাইটের ১৫ মিলিয়ন আইপডে রাখা যাবে। এই প্রজেক্টে ব্যবহৃত অপটিকাল ফাইবার (চুলের ১০ ভাগের এক ভাগ পাতলা) দিয়ে পুরো পৃথিবীকে ২ বার মোড়ানো যাবে। এর নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত সুপার কম্পিউটার কোনো কিছু বিশ্লেষণ করতে প্রতিসেকেন্ডে ১ বিলিয়ন ট্রিলিয়ন অপারেশন করতে পারবে, যা বর্তমান সুপার কম্পিউটার থেকে ১০০০ গুণ দ্রুত।
গ্রাহকরা মোবাইল ফোনে যে ইন্টারনেট ব্যবহার করে, সেটি কিন্তু আনলিমিটেড নয়। মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় থাকে। ১. ইন্টারনেট স্পিড ২. ডাটার লিমিট ও সময়। অর্থাৎ ১ জিবি ইন্টারনেট কিনলে সেই পরিমাণ ডাটা ডাউনলোড বা আপলোড করা যায়। সেটি ১ ঘণ্টায়ও শেষ হতে পারে কিংবা মোবাইল কোম্পানি থেকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া সময়ের মধ্যে। এটির গতি মোবাইল সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছা অনুযায়ী হয়ে থাকে।
তবে মোবাইল ফোনে কথা বলার সময় বারবার লাইন কেটে যাওয়ার বিষয়টি কভারেজ অনুপাতে অতিরিক্ত সিম ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে। উল্লেখ্য, কথার মাঝখানে বারবার সংযোগ ছিন্ন হাওয়াকে ‘কল ড্রপ’ বলে। গত এক দশকে দেশে মোবাইল সংযোগের সংখ্যা যে গতিতে বেড়েছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়েনি পরিকাঠামো। তা সে হোক স্পেকট্রামের পরিমাণ বা টাওয়ারের সংখ্যা। আছে ৩জি, ৪জি বা ৫জি’র অসঙ্গতিও। এরপরও প্রতিদিন ফুটপাতে ও মোবাইলের দোকানে হাজার হাজার নতুন সিম বিক্রি হচ্ছে। আবার ব্রাউজিং করার ফলে প্রতিনিয়ত মোবাইলে প্রচুর তথ্য সংরক্ষিত হচ্ছে। এতেও মোবাইলের স্পিড কমে যাওয়ায় ‘কল ড্রপ’ ঘটে।
এছাড়াও দেশে এবং বিশ্বব্যাপী মোবাইল ব্যাংকিং প্রচলন হওয়ায় গ্রাহকরা এখন ক্রমে ক্রমে মোবাইল ব্যাংকিংয়ে অভ্যস্ত হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে ছোট-বড়, ধনী-গরিব সকলেই মোবাইল ব্যাংকিংয়ের আওতায় চলে আসবে। এমতাবস্থায় সর্বক্ষেত্রে একটি নিরবচ্ছিন্ন, নিরাপদ ও দ্রুত গতির ডেটা ট্রান্সফার তথা মোবাইল যোগাযোগের অবকাঠামো নিশ্চিত করা সময়ের দাবি। তাই ডব্লিউডিএম প্রযুক্তিটি বাণিজ্যিকভাবে চালু হলে তথ্য আদান-প্রদানে বিশ্বব্যাপী মোবাইল গ্রাহকদের মধ্যে নেমে আসবে স্বস্তি।
লেখক : অধ্যাপক এবং তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, আইআইটি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।








