প্রকাশ : ২০ জুলাই ২০২৫, ০১:০৪
খণ্ডে খণ্ডে অখণ্ড জীবন
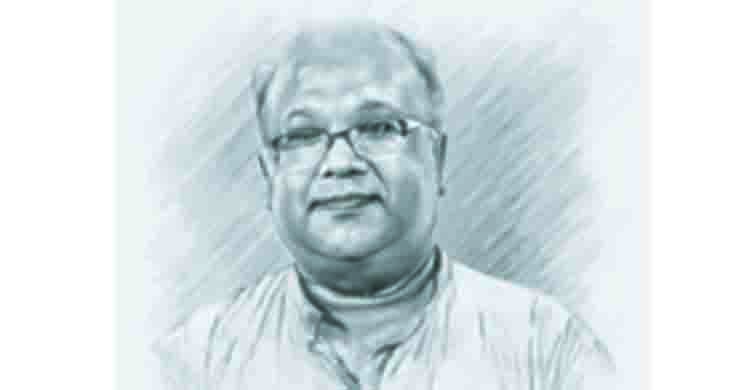
(পঁয়ত্রিশতম পর্ব)
রোগীদের আমি আমার রোগীরা :
মায়ের গর্ভে যেমন সন্তান না আসলে নারীত্বের পূর্ণতা আসে না, তেমনি একজন চিকিৎসকের কাছেও রোগী না আসলে চিকিৎসক জীবনের পূর্ণতা লাভ হয় না। মেডিকেল কলেজের জীবনে ইন্টার্নশিপ করাকালীন আমার দায়িত্বে পঁাচটা বেডের রোগী দেওয়া হয়েছিলো সার্জারি ওয়ার্ডে। ইউরোলজির অধ্যাপক ডা. ওমর ফারুক ইউসুফ স্যারের অধীনে আমার সার্জারি ওয়ার্ড শুরু হয়। আমাদের সিএ ছিলেন খোরশেদ ভাই। আমার বেডে একটা রোগী পেয়েছিলাম, যিনি ডাকাতি মামলার আসামি ছিলেন এবং বাড়ি ছিলো বঁাশখালি। তাকে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের হাসপাতাল থেকে রেফার করা হয়েছিলো। ডাকাত রোগীটার পেটের অন্ত্রে পার্ফোরেশন হয়েছিলো। অর্থাৎ অঁাত ফুটো হয়ে গিয়েছিলো। এর মূল কারণ ছিলো অতি মাত্রায় ডাই-ক্লোফেনাক জাতীয় ব্যথার ঔষধ সেবন। অপারেশনের আগে রোগীর দু ব্যাগ রক্ত রেডি রাখার কথা ছিলো। কিন্তু রোগীর স্বজনেরা কেউ ছিলো না বিধায় আমাকেই দু ব্যাগ রক্ত জোগাড় করতে হয়েছিলো। পাশাপাশি রোগীকে অ্যানিমিয়া কারেকশন করতে গিয়ে নিজের পয়সায় হেমাক্সিল কিনে শিরায় ঢুকিয়েছি। ওটি তালিকা থেকে যাতে বাদ না পড়ে সেজন্যে প্রয়োজনীয় সকল ঔষধ রেডি করে দিতে হয়েছিলো আমার নিজের তাগিদে। কিন্তু ডাকাত রোগীটার রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল ছিলো বিধায় তার অপারেশন-ক্ষত শুকোতে বেশ দেরি হয়েছিলো। আমাকে টানা চৌদ্দ দিন নিয়মিত তার অপারেশনজনিত ক্ষতস্থানে ড্রেসিং করতে হয়েছিলো। তার আরোগ্য ও স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের স্বার্থে মাথার চুল কামিয়ে বেল করে দেওয়া হয়েছিলো। এই ব্লেডটাও আমার নিজের টাকায় কেনা। পরবর্তীতে তাকে ভরাপেটে ঔষধ খাওয়ানোর জন্যে দুয়েকবার নিজেই বিস্কুট কিনে দিতে হয়েছিলো। সুস্থ হয়ে ছাড়া পেয়ে যাওয়ার দিন দুয়েক আগে রোগীটা তার স্ত্রীর কাছে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো তার বাপ বলে।
মিডল্যান্ড হাসপাতালে একটা বাচ্চা রোগী নিয়ে সারারাত জাগতে হয়েছিলো। ডিপথেরিয়াজনিত জটিলতায় বাচ্চাটা মারা যায়। রাতের এমন সময়ে রোগীটা আসে যখন আর উন্নত স্থানে পাঠানোর সুযোগ ছিলো না। বাধ্য হয়েই মিডল্যান্ডে তাকে রাখতে হয়েছিলো বঁাচানো যাবে না জেনেও। পলি ক্লিনিকে নাইট ডিউটি করার সময় একটা রোগী পেলাম, যার অভিযোগ ছিলো পেট ভরে গরুর মাংস খেয়ে মন ভরে অ্যালকোহল সেবন। তার পরিণামে তীব্র পেট ব্যথা। এ রোগীও সারারাত জাগিয়ে রেখেছিলো বিবিধ জটিলতায়। এভারগ্রিন ক্লিনিকে সন্ধ্যার ডিউটিতে পেলাম একটা কিশোর রোগী, যার সারা গায়ে লাল ছোপ ছোপ রক্ত জমাট বঁাধার দাগ। অধ্যাপক এম এ হাসান চৌধুরী স্যারের রোগ নিরূপণ ছিলো অসাধারণ। তিনি রোগীকে পলিসাইথেমিয়া ভেরা’র রোগী হিসেবে শনাক্ত করে দু ব্যাগ রক্ত তার শরীর থেকে টেনে ফেলে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেননা, তার রক্তে লোহিত রক্ত কণিকার পরিমাণ এতো অধিক ছিলো যে, রক্তের সান্দ্রতা ও গাঢ়ত্ব ছিলো অস্বাভাবিক রকমের বেশি। ফলে রক্তনালীর ছিদ্র দিয়ে স্বাভাবিক রক্ত সঞ্চালন সম্ভব হচ্ছিলো না। এতে কিশোরটি শ্বাসকষ্টে ভুগছিলো। স্যারের কথা মোতাবেক দু ব্যাগ রক্ত টেনে নিতেই তার শ্বাসকষ্ট কমে গেলো এবং কিশোরটিকে আমরা নির্বিঘ্নে চিকিৎসার পরবর্তী ধাপের জন্যে উচ্চতর চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলাম।
ব্যক্তিগত চেম্বারে রোগীরা এসে তাদের নিজ নিজ ভাষ্যে রোগের বিবরণ দেয়। এতে রুগ্ন জীবনের ভাষাশৈলি উন্মোচিত হয়। একজন রোগীর অভিযোগ ছিলো, ‘ স্যার, আমার পিঠে কেউ যেন এসি ফিট করে দিছে।’ তার বিস্তারিত সাক্ষাৎকার নিয়ে পরে জানা গেল, আসলে তার পিঠের একটা বিশেষ জায়গায় শীতলতা অনুভূত হয়। রোগীর এই ভাষ্য থেকে সহজেই রোগ নিরূপণ করা গেলো। রোগীটা আসলে তার স্নায়ুতন্ত্রের সমস্যায় ভুগছিলো। একজন মধ্যবয়স্ক নারী রোগী এসে অভিযোগ করে বললেন, স্যার, আমার মাথার মজলিশ নষ্ট হয়ে গেছে। অনেক কষ্টে পরে তথ্য আদায় করে বুঝতে পেরেছিলাম, রোগীর আসলে মাথার মধ্যে অবর্ণনীয় অস্বস্তি তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ তার সেরিব্রামে অক্সিজেন সরবরাহ কমে যাচ্ছিলো বলে প্রতীয়মান হয়। একজন চরের বাসিন্দা মহিলা রোগীর অভিযোগ ছিলো, তার পেটে গাঙের জোয়ারের মতো ডাক উঠে। পরে অবশ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ধরা পড়ে, তার পাকস্থলীর নির্গম পথে টিউমার হয়েছে। পায়ে ব্যথা পাওয়া এক রোগীর অভিযোগ ছিলো, তিনি মধ্যরাতে কঁাড় থেকে পড়ে গেছেন। আমি স্থানীয় ভাষা বুঝতে অপারঙ্গম ছিলাম বিধায় ধরে নিয়েছিলাম তিনি কার দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। পরে আরও খোলাসা করার জন্যে জিজ্ঞেস করায় জানতে পেরেছিলাম, তিনি ঘরের ভেতরে ছাদ (সিলিং) থেকে জিনিস পাড়তে গিয়ে পড়ে গেছেন। অধিকাংশ রোগীর ভাষায় একটা অভিযোগ আকচার পেতাম। তা হলো খাইয়া যায়, লইয়া যায়। হাত দিয়ে দেখাতে বলার পর বুঝতে পেরেছিলাম, আসলে তাদের পায়ের মাংসপেশি ও স্নায়ুর দুর্বলতা আছে।
কক্সবাজার এলাকার এক রোগীর অভিযোগ ছিলো, তার কুসুমে পানি জমেছে। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পরে পরিষ্কার হলো, ঐ রোগীর স্ক্রোটামে বা অন্ডকোষের থলিতে পানি সঞ্চয়ন হয়েছে। রাজরাজেশ্বরের এক চাচা রোগী ছিলেন, যিনি ভোর পঁাচটায় ফোন দিতেন, কাকা, আজ চেম্বারে বসবেননি। তিনি মনে করতেন, তার জন্যে সকাল হওয়া মানেই ডাক্তারেরও সকাল হওয়া। একজন পল্লি চিকিৎসক ছিলেন, ঢালী ভাই। তিনি রাত দুটোয় ফোন দিতেও কার্পণ্য করতেন না। খুব ছোট ছোট সমস্যার জন্যেও রাত দুটোয় ফোন দিতেন। তার চিন্তায় এটা থাকতো না, রাত দুটো মানে অনেক রাত। রোগীদের হাতে ডাক্তারের ফোন নম্বর দেওয়ার আরও নানা ধরনের বিপদ আছে। একদিন বিকেলে চারটার দিকে চেম্বার সেরে এসে দুপুরের আহার বিকেলে খেতে বসেছি সপত্নী। এ সময় এক রোগীর ফোন এলো। ফোন ধরতেই ও প্রান্ত থেকে আওয়াজ ভেসে এলো, স্যার, আমার পায়খানাটা হঠাৎ বিজলা বিজলা হইতেছে। অথচ তখন মাত্র আমি আমার প্রথম গ্রাস মুখে দিয়েছি। আমার মুখ দিয়ে প্রতিক্রিয়াজনিত কারণে বের হয়ে গেলো, বলেন কী! বিজলা বিজলা! আমার কথা শুনে আমার পত্নী আর ভাত খেতে পারেননি। আমিও পড়লাম বেকায়দায়। কোনো কোনো পল্লি চিকিৎসক আছেন, রাতের দুটোয় ফোন দিয়ে বলবেন, স্যার কি ঘুম আসতেছেন? তখন মেজাজ খারাপ করে মনে মনে বলি, ব্যাটা মস্করা করিস্? ঘুমে জাগিয়ে বলিস্, ঘুম আসতেছেন? আর কেউ কেউ রাত দুপুরে ফোন দিয়ে বলে, স্যার, আমার পরিবারের পেট ব্যথা। কী দেওয়া যায়? তাকে বলি, ভোল্টালিন সাপোজিটরি দেন। বলে, ওটা নেই। বলি, অ্যালজিন ট্যাবলেট দেন। বলে, তাও নেই। তাহলে নাপাডল ট্যাবলেট দেন। বলে, তা-ও নেই। তখন বাধ্য হয়ে বলি, কী আর করবেন, আমার নাম করে একটা ফুঁ দেন। ও প্রান্ত থেকে জবাব আসে, স্যার, একটা গ্যাস্ট্রিকের ঔষধ খাওয়াই? তখন বাধ্য হয়েই বলি, আপনি নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখে আমাকে ফোন দিলেন কেন?
কিছু কিছু গ্রামের রোগী আছেন, যাদের অতি জরুরি অবস্থার জন্যে মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে। তারা ফোন করে বলে, স্যার, রোগীর তো ঘুম হয় না, কী খাওয়াবো? তখন কোনো ঔষধের কথা বললে তারা লাইনে রেখে বলে, স্যার আমার পোলাডারে কন্। ছেলেটাকে বললে পরে, সে খাতায় লেখে কিন্তু আবার বলে, স্যার, বাজারে গিয়ে দোকানদারের সামনে থেকে ফোন দিলে একটু বইলেন। এই হলো আমরা যারা রোগীকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার চেষ্টা করি, তাদের অবস্থা। কিছু কিছু রোগী আছেন, স্নেহ করেন অকারণ। নিউ মার্কেটের মোতালেব সাহেবের শ্বশুর-শাশুড়ি আমার রোগী ছিলেন। প্রতিবছর তারা আমাকে তাদের গাছের আম খাওয়াতেন। নাছির তালুকদার ছিলেন বাবুরহাটের দাসাদীর অধিবাসী। গ্রাম্য ডাক্তার। তিনিও আমাকে তার বারোমাসী আম খাওয়াতেন বছরে একবার। রাজরাজেশ্বরের হোসেন বেপারী চাচা আমাকে লাল আউশ চাউল খাওয়াতেন প্রতি বছর। কিছু কিছু পল্লি চিকিৎসক আছে টাউট টাইপের। এরা রোগী আনলে বার বার রোগীকে চাপ দেয়, স্যারকে সবকিছু খুলে বলেন। রোগীও না বুঝে তার একটার পর একটা সমস্যার কথা বলতে থাকে। আর পল্লি চিকিৎসক এই ফঁাকে অদরকারি পরীক্ষা-নিরীক্ষার তালিকা দীর্ঘ করে। শাহ্ আলম নামে এরকম এক লোক একবার আমাকে দেখানোর জন্যে একজন রোগী এনেছিলো। কাউন্টারে গিয়ে আমি যা পরীক্ষা দেইনি, রোগীকে বুঝিয়ে তার অধিক পরীক্ষা সে করিয়ে নিলো। আমি জানতে পেরে তাকে বকলাম বেশ। অথচ রিপোর্ট দেখিয়ে যাওয়ার সময় রোগীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে গেলো, স্যার আমার নিজের মানুষ, একশো টাকা ফিস কম রাখবেন। এ কথার পর রোগীর কাছে শাহ্ আলম হয়ে গেলো আপনজন। কারণ সে রোগীর হয়ে ডাক্তারকে ভিজিট একশো টাকা কম দিয়েছে। অথচ বুঝলো না, এই লোকই তার আরও হাজার পঁাচেক টাকা অতিরিক্ত খরচ করিয়ে নিজে তার অর্ধেক বাগিয়ে নিলো রিসিপশান থেকে। যতোই বলি, নিজেরা সরাসরি আসবেন, তবুও রাত-বিরেতে তাদের এলাকায় কাছে পায় বলে এরাই তাদের আপনজন। যতো ঠকাক না কেন।
এক মুরুব্বি রোগী ছিলেন, তার নাম খেয়াল না পড়লেও সবাই তাকে বাহাদুরের মা বলেই সম্বোধন করতো। তিনি প্রতি সপ্তাহে একবার কোনো সমস্যা না থাকলেও আমাকে দেখাতে আসতেন। আসলে দেখাতে আসতেন না, বরং আসতেন আমাকেই দেখতে। আমার ওপর তার পুত্রস্নেহ বর্ষিত হয়েছিলো। একজন মজার রোগী ছিলেন মোতালেব মাস্টার। তিনি ঢাকা-কুমিল্লা যেখানেই চিকিৎসা নেন না কেন, আমার কাছে এসে নতুন করে রোগ ও ঔষধ বুঝে নিয়ে যেতেন। অবশ্যই পূর্ণ ভিজিট দিয়ে। স্ট্রোকের রোগী আশেক আলী। ঢাকা ফেরত রোগী। ভ্যান গাড়িতে করে বিজয় গোপালের মাধ্যমে আমার চেম্বারে এসেছিলেন। চিকিৎসায় নব্বই ভাগ পূর্বাবস্থা ফিরে পান। তিনি মাসে একবার আসতেন তবুও আমার কাছে। হাতে বটে নিয়ে আলগোছে একশ টাকা করে দিয়ে যেতেন প্রতিবার। বুঝতাম, এটা রোগীর ফি নয়, এ ছিলো অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা।
মাঝে মাঝে প্রেসক্রিপশন সার্ভ করতে গিয়ে দোকানে নিযুক্ত কর্মচারীরা আমাদের বিপদে ফেলতো তাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের বৃহৎ প্রয়োগ দেখিয়ে। এদের কারুরই শিক্ষা তেমন পোক্ত নয়। প্রেসক্রিপশনে পরিষ্কার লেখা ছিলো ফিডাপ্লেক্স। কিন্তু তাদের প্রবণতা হলো প্রথম অক্ষর দেখেই ঔষধ বুঝে ফেলা। ফলে মনোযোগ দিয়ে না পড়ে প্রথম অক্ষর দেখেই রোগীকে দিয়ে দিলো ফাইডোপা। একটা ভিটামিন ইঞ্জেকশনের স্থলে উচ্চ রক্তচাপ কমানোর ঔষধ দিয়ে রোগীর বারোটা প্রায় বাজিয়েই দিয়েছিলো। ভাগ্যিস্ রোগী আমাকে দেখাতে এসেছিলেন ঔষধ ঠিক আছে কি না। নচেৎ কী কেলেঙ্কারিই না হতো! চরের অধিবাসী এক বয়স্ক মানুষ আমার দীর্ঘদিনের রোগী। তার মন জয় করতে আমার যথেষ্ট মনোযোগ ব্যয় করতে হয়েছে। আমার চিকিৎসায় সন্তুষ্ট এই রোগী একদিন তার কিশোরী মেয়েকে চিকিৎসার জন্যে আনলেন। তার অভিযোগ ছিলো দুপায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে সবসময়। দেখে মনে হলো তার দুপায়ের রক্তনালীতে রক্ত সঞ্চালন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাকে সমাধান হিসেবে ডায়াস্মিন-হেসেপেরিডিন খেতে দিলাম একটা করে দুবেলা। ঔষধটি যেমন রক্তক্ষরণধর্মী পাইলস্ রোগে দেওয়া যায়, তেমনি শরীরের প্রান্তীয় অঞ্চলের রক্তবাহিকা সমূহের রক্তসঞ্চালন উন্নত করতেও ব্যবহার করা হয়। কিন্তু দোকানে যখন তিনি ঔষধ কিনতে গেলেন, তখন দোকানের অপরিপক্ক অর্ধশিক্ষিত কর্মচারী জিজ্ঞেস করলেন, আপনার মেয়ের কি পাইলস্ রোগ বা অর্শ রোগ আছে? রোগীর বাবা এতে স্বাভাবিকভাবেই আশ্চর্য হয়ে বললেন, কেন? তখন ঐ কর্মচারী বলেছিলো, না, ডাক্তার মনে হয়ে তাহলে ভুল অষুধ লিখেছে। আপনি ডাক্তারকে ফোন দেন। তখন ঐ অভিভাবক আমাকে ফোন করে তার ক্ষোভ ঝাড়লেন। ডাক্তার সা’ব, আমি আপনার চিকিৎসায় সুস্থ হওয়ায় আমার মেয়েকে আনছিলাম দেখাইতে। আর আপনি কি না আমার মেয়েকে ভুল অষুধ দিলেন? তাকে পায়ের ঝিন ঝিন রোগের জন্যে পাইলসের অষুধ দিলেন? আমি তার কথা শুনে বুঝে গেলাম, এটা হলো দোকানের না পড়ে লন্ডন হতে এমআরসিপি পাস করা বড়ো ডাক্তার অর্ধশিক্ষিত কর্মচারীর কাজ। তখন বাধ্য হয়েই বললাম, ঐ কর্মচারীকে বলেন, যাতে সে গুগল করে এই ঔষধের কোন্ কোন্ রোগে ব্যবহার আছে তা জেনে নেয়। এই ঔষধের দ্বিতীয় নাম্বার ব্যবহারেই লেখা আছে, ঔষধটি পায়ের দুর্বল রক্ত সঞ্চালনকে সবল করতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তিনিও তো শিক্ষাহীন। কাজেই দোকানের কর্মচারী তাকে যে ভুল তথ্য দিয়ে ভয় লাগিয়েছে সেই তথ্যকেই তিনি শুদ্ধ বলে মেনে নিলেন। ফলে আমি আর ঐ রোগীকে চেম্বারে পাইনি এর পর থেকে। একই রকমের ঘটনা ঘটেছে আমার মেজদির সাথেও। তিনিও দঁাতের ব্যথায় কষ্ট পেয়ে আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, কী খাবেন। আমি তঁাকে ব্যথার একটা ঔষধ খেতে বলার পাশাপাশি ফ্ল্যাজিল ট্যাবলেট খেতে বলেছিলাম দিনে তিনবার সাতদিন যাতে ব্যথার জন্যে দায়ী জীবাণু মারা যায়। তিনি আমাকে একচোট বকা দিলেন। তিনি রেগে বললেন, তুই তো রোগী মেরে ফেলবি। ভালো করে শুনে চিকিৎসা দে। দঁাতের ব্যথায় পাতলা পায়খানার ঔষধ খাবো কেন? তঁাকে আমার বুঝাতে কষ্ট হয়েছে যে, আমাদের মুখগহ্বর আমাদের মলদ্বারের চেয়েও অধিক জীবাণুময়। পাতলা পায়খানার জন্যে যে জীবাণু দায়ী, দঁাতের কতিপয় ইনফেকশনেও একই জীবাণু দায়ী। কাজেই একই ঔষধে দঁাতের জীবাণুও নির্মূল হয়। এরকম একজন প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক পেয়েছিলাম যিনি আমার প্রেসক্রিপশনে একটা ঔষধ কিনে খাওয়ার আগে ঔষধের সাথ দেওয়া লিটারেচার নিয়ে আমাকে একচোট নিলেন। বললেন, দাদা, এই ঔষধের এতো এতো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। তবুও আমাকে তা খেতে প্রেসক্রাইব করলেন! বললাম, আপনি সব ঔষধেরই কোনো না কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পাবেন। এমনকি প্যারাসিটামলেরও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে। তাই বলে ঔষধের লিটারেচার পড়ে ঔষধ খেতে গেলে জীবনে কোনো ঔষধই আপনার আর খাওয়া হবে না। আমরা ডাক্তারেরা ঔষধ লেখার আগে যাচাই করি, উপকার আর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার অনুপাতের ভারসাম্য কেমন। যদি দেখি উপকারের পাল্লা ভারী, কেবল তখনই ঐ ঔষধটা লিখি। একজন ডাক্তারই ভালো জানবেন, কোন্ ঔষধটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হবে জেনেও আপনাকে খাওয়াতে হবে। সুতরাং ঔষধের সাথে দেওয়া লিটারেচার পড়লে জীবনে কোনো রোগ নিরাময়কারী ঔষধই নিশ্চিন্তে সেবন করা যাবে না।
একবার পুরাণবাজারের এক পুরানো রোগী জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজনে বুকে ব্যথা নিয়ে আমার চেম্বারে আসলেন। ইসিজি করে আমি দেখলাম, তিনি হার্ট অ্যাটাকের রোগী এবং এই হার্ট অ্যাটাক মাত্র কয়েকঘন্টা হলো শুরু হয়েছে। আমি তাকে তাড়াতাড়ি সেন্ট্রাল হাসপাতালে রেফার করলাম। কারণ তার দ্রুত অক্সিজেন থেরাপি দরকার। জেনারেল হাসপাতালে যাওয়ার চেয়ে সেন্ট্রাল হাসপাতালে গেলে দ্রুত অক্সিজেন থেরাপি পাবে। তখন ছিলো ডিসেম্বর মাস এবং মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা চলছিলো। হাসান আলী স্কুলের মাঠ সংলগ্ন রাস্তায় বঁাশের ব্যারিকেড দিয়ে ওয়ান ওয়ে করে তোলা হয়েছিলো। ফলে ঐ রোগী ঘুরপথে সেন্ট্রাল হাসপাতালে যেতে একটু বেশি সময় লেগে যায়। এরমধ্যেই রোগী মারা যায়। কিছুক্ষণ পর রোগীর লোকজন আমার চেম্বারে এসে তীব্র চোটপাট নেওয়া শুরু করলেন। কেন চেম্বারে অক্সিজেন নেই। বললাম, চেম্বারের ব্যবস্থা জরুরি রোগীর সেবা দেওয়ার জন্যে নয়। এখানে রুটিন কেস কিংবা দীর্ঘদিন ধরে ভোগা রোগীদের চিকিৎসা দিয়ে আরোগ্য করা হয়। জরুরি রোগীর জন্যে বেড দরকার, নার্স দরকার, আয়া-ওয়ার্ডবয় দরকার। জরুরি ঔষধের জন্যে ফার্মেসিও দরকার। এসবকিছু একটা চেম্বারে রাখা সম্ভব নয়। ডাক্তারের চেম্বার চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকে না। কয়েক ঘন্টা খোলা থাকে। কাজেই এখানে অক্সিজেন সিলিন্ডার রাখা সম্ভব নয়। এসব আয়োজন যেখানে সেখানে রাখাও যায় না। অনুমতি নেই। আমার কথায় তাদের মারমুখী ভাব কমলেও ক্ষোভ কমেনি। আমিও মার খাওয়া থেকে রেহাই পেয়ে হঁাফ ছাড়লাম। ভাবলাম, কত অনিরাপদ একজন ডাক্তারের পেশা!
রোগীর লোকজন এই খুশিতে মাথায় তোলে, আবার এই ক্ষোভে গায়ে হাত তোলে। অথচ চিকিৎসার স্বাধীনতা না পেলে ডাক্তারের পক্ষে কোনো রোগীকে সারিয়ে তোলা সম্ভব নয়। ডাক্তারের চেম্বারে নিরাপত্তার খাতিরে আনসার রাখাও সম্ভব নয়। আজ আপনি আমাকে আঘাত করলেন আপনার রোগীর অবস্থা খারাপ হওয়ার জন্যে, আর আগামীকাল আরেকজন রোগী সেবা পাবে না সেই ভীতির কারণে। কাজেই যে কোনো কাজ পরিণাম ভেবেই করতে হয়। ডাক্তার যদি শতভাগ রোগীকে সারিয়ে তুলতে পারতো তবে পৃথিবী তো মৃত্যুশূন্য হয়ে পড়তো। কিন্তু বাস্তবে কি তা সম্ভব? আপনি যে অবহেলার দায় ডাক্তারের ওপর চাপান, সেই একই অবহেলার দায় আপনার ওপরও বর্তায়। কেননা আপনি বা আপনারা রোগীকে যথাসময়ে হাসপাতালে আনলে অনেক রোগী মৃত্যুকে অকালে বরণ করতো না। আপনার দেরির কারণে কখনও কখনও ডাক্তারেরও কিছু করার থাকে না। পরে অবশ্য ঐ রোগীর লোকজন আমার চেম্বারে এসে তাদের সেদিনের আচরণের জন্যে লজ্জিত হয় ও দুঃখপ্রকাশ করে। চারদিন পর মৃত রোগীর পারলৌকিক অনুষ্ঠানে যাওয়ার আমন্ত্রণও পাই। (চলবে)
চঁাদপুর।








